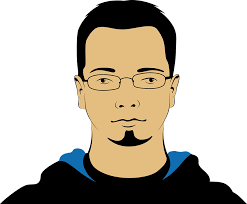

এফএনএস এক্সক্লুসিভ: কোনোভাবেই শৃঙ্খলায় আনা সম্ভব হয়ে উঠছে না রাজধানীর গণপরিবহণ। নগর পরিবহণ বা বাস রুট রেশনালাইজেশনের উদ্যোগও থমকে গেছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট কমিটির এতদিন নিয়ম মেনে সভা হলে সেটিও এখন আর হচ্ছে না। অন্যদিকে ৫ আগস্টের পর পটপরিবর্তনে পরিবহণ খাতের নেতৃত্বেও আসে হাতবদল। নতুন করে ঢাকা সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির দায়িত্ব নিয়েই বাস রুট রেশনালাইজেশনকে পাশ কাটিয়ে বিভিন্ন রুটে চলা বাসগুলো শৃঙ্খলায় আনতে রং এবং কাউন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়। প্রথম রুট হিসেবে আবদুল্লাপুর হয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করা সব বাসের রং নির্ধারণ করা হয় গোলাপি। তবে আশার আলো জাগানো গোলাপি বাসও হতাশায় ডুবিয়েছে। সপ্তাহ পার না হতেই সামনে আসতে থাকে নানা সমস্যা। রাজধানীর আবদুল্লাপুর হয়ে গুলিস্তান পর্যন্ত সড়কটিতে দেখা গেছে, এই রুটে চালু হওয়া গোলাপি রঙের বাসসেবা শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম। সব জায়গায় নেই পর্যাপ্ত কাউন্টার। আব্দুল্লাহপুর থেকে বনানী, মহাখালী রুটে কিছু কাউন্টার থাকলেও কুড়িল থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত দেখা মেলে না কোনো কাউন্টারের। কাউন্টার না থাকায় ই—টিকিটিং ব্যবস্থাও চালু হওয়ার আগেই বন্ধ। ফলে আগের মতোই যত্রতত্র চলছে যাত্রী ওঠানামা। রয়েছে ভাড়া বেশি নেওয়ারও অভিযোগ। শুরুর দিন অল্পসংখ্যক বাস দিয়ে চালু করা এসব পদ্ধতি দ্রুত পুরোদমে চালুর আশ^াস দিয়েছিলেন ঢাকা সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির নেতারা। কিন্তু দেখা গেছে, ঢাকার গণপরিবহণে শৃঙ্খলা ফেরাতে চালু করা কাউন্টার ও ই—টিকিটিং ব্যবস্থা কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর—আব্দুল্লাহপুর থেকে ছেড়ে আসা ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলাচল করা ২২টি কোম্পানির ১০০টি বাস নিয়ে কাউন্টার ও ই—টিকিটিং ব্যবস্থা চালু করে ঢাকা সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতি। শুরুতে কোম্পানিগুলো নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রি করে যাত্রী পরিবহণ করছিল। এতে যাত্রীরা গণপরিবহণে শৃঙ্খলা ফেরার আশার আলো দেখেছিল। কিন্তু সপ্তাহ পার হতে না হতেই চালক ও শ্রমিকদের আপত্তি তোলে। পরবর্তীতে কোম্পানিগুলো লস হচ্ছে জানিয়ে কাউন্টার ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়। এখন অধিকাংশ বাস আগের মতোই চলাচল করছে, যেখানে—সেখানে যাত্রীদের রাস্তা থেকে উঠানো হচ্ছে এবং নগদ টাকা আদায় করা হচ্ছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যাত্রীরা নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে বাসে ওঠেন, ফলে বাস স্টাফদের হাতে ভাড়া তোলার সুযোগ থাকছে না। বরং ট্রিপপ্রতি বাস চালক ও হেল্পারের জন্য কোম্পানি ভেদে ৩০০ থেকে ৬০০ টাকা মজুরি নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বাস স্টাফদের দাবি, এতে তাদের আয়ে বড় ধরনের ধস নেমেছে। আগে বিশৃঙ্খলভাবে চললেও দৈনিক তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত উপার্জন সম্ভব হতো, কিন্তু এখন দিনে হাজার টাকাও থাকছে না। তাই নতুন ব্যবস্থায় আসতে রাজি না তারা। পরিবহণ শ্রমিকদের ভাষ্য, ঢাকার অধিকাংশ বাস চুক্তিভিত্তিক পরিচালিত হয়, যেখানে চালক ও শ্রমিকরা দৈনিক জমা ও তেলের খরচ পরিশোধের পর বাকি অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। এতে কোম্পানি ভেদে বাস মালিকরা তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা পান, আর বাস স্টাফরা পান চার থেকে পাঁচ হাজার। আর এ কারণেই তারা প্রতিযোগিতা করে বেশি ট্রিপ দিতে চান, যত্রতত্র যাত্রী তোলেন। এতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে, যাত্রীদের হয়রানির শিকার হতে হয়। একাধিক কোম্পানির চালকরা জানান, পরিবহণ সেক্টরে চালকরা একদিন বিরতি দিয়ে গাড়ি চালান। তাই বর্তমানে নতুন ব্যবস্থায় ড্রাইভার ও স্টাফ মিলিয়ে দিনে দুই তিন ট্রিপে দুই হাজার—পঁচিশ শত টাকা পাওয়া যায়। এর মধ্যে দুপুরের খাবারের খরচ নিজেদের। ওই খরচ বাদ দিলে থাকে ১২শ—১৫শ টাকা। দুই দিনের হিসাবে তা আরও কমে আসে। তাই তারা কাউন্টার ব্যবস্থায় আগ্রহী না। এদিকে নতুন ব্যবস্থায় কিছু কিছু বাস কোম্পানির আপত্তি রয়েছে। কোম্পানিগুলো থেকে জানায়, কাউন্টার ব্যবস্থায় বাসগুলো যত্রতত্র লোক উঠানো বন্ধ করছে না। ফলে সব ভাড়া কাউন্টারে জমা পড়ছে না। এতে দিনশেষে কোম্পানির মোট আয় অনেক কমে গেছে। এই আয় থেকে বাস স্টাফদের খরচ বাদ দিলে বাস মালিকদের দেওয়ার মতো কিছু থাকে না। আগে বাস মালিকরা গড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা আয় করতে পারলেও নতুন ব্যবস্থায় তাদের ভাগে এক হাজার টাকা করে পড়ে। তবে অভিযোগ রয়েছে, কাউন্টার ও ই—টিকিটিং ব্যবস্থার কারণে কোম্পানির পরিচালকদের নিয়মবহিভূর্ত আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি বাস মালিকদের থেকে কোম্পানি পরিচালনা জন্য দৈনিক ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা জমা নেয়। এতে কোম্পানি পরিচালনার খরচ উঠেও বাড়তি অনেক টাকা থাকে যা পরিচালনা পর্ষদ নিজেরা ভাগাভাগি করে নেয়। এছাড়াও ওয়েবিল চেকারদের কাছ থেকে দৈনিক গড়ে ১৫ হাজার টাকার মতো নিয়ে থাকে কোম্পানির লোকেরা। যা তাদের নিজেরা রেখে দেয়। কোম্পানি পরিচালনার সঙ্গে এই আয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু কাউন্টার পদ্ধতিতে কোম্পানির জন্য নির্দিষ্ট খরচ রাখা বাদে বাকি টাকা বাস মালিকদের কাছে যাবার কথা। এদিকে কাউন্টার পদ্ধতিতে পরিবহণ খাতের চাঁদাবাজরাও নাখোশ। ই—টিকিটিংয়ের কারণে যাত্রীদের ভাড়ার টাকা বাস স্টাফদের হাতে থাকে না। আর এই কারণ দেখিয়ে মোড়ে মোড়ে চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন বাস স্টাফরা। আর অভিযোগ রয়েছে এই চাঁদাবাজদের সঙ্গে কোম্পানি ও পরিবহণ মালিক সমিতির সুবিধাবাদী লোকেরাও জড়িত। তাই সবাই যোগসাজশে কাউন্টার ব্যবস্থার বিরোধিতা করে তা উঠিয়ে দিতে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গণপরিবহণে শৃঙ্খলা ফেরাতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মো. হাদিউজ্জামান বলেন, সরকার যদি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গণপরিবহণ চালু করে, তাহলে এই সমস্যা সমাধান হতে পারে। সরকারের পক্ষ হতে কোম্পানিভিত্তিক একটা বিজনেস মোডিউল তৈরি করতে হবে, যেখানে বাস মালিকরা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে। বিদ্যমান ব্যবস্থা জিইয়ে রেখে শৃঙ্খলা আনা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, এর জন্য প্রয়োজন অন্তত ৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। এই টাকায় ঢাকার যত বাস আছে, সব কিনে নিয়ে ভালোগুলো রেখে বাকিগুলো ভেঙে ফেলা এবং কোম্পানিতে দক্ষ জনবল নিয়োগ করা। ঢাকায় ২০ শতাংশ যাত্রী বহনের জন্য যদি ৩০ হাজার কোটি টাকা দিয়ে একটি মেট্রোরেলের লাইন তৈরি করা যায়, তাহলে বাকি যাত্রীদের সুবিধার্থে ৪ হাজার কোটি টাকা বেশি নয়। ঢাকা সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. সাইফুল আলম বলেন, গোলাপি বাসে পুরোপুরি সমস্যার সমাধান করতে এক থেকে দেড় মাসের মতো সময় লাগবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে গাড়ি রং করাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাথমিকভাবে আমরা জোর দিয়েছে নির্দিষ্ট স্থান থেকে যাত্রী বাসে ওঠানো বা টিকিট বিক্রি নিয়ে। তিনি বলেন, সিটি করপোরেশন তো কোনো দায়িত্বই নিচ্ছে না। এখন আমরা নিজেরা যদি বাস স্টপেজের সাইন লাগাতে যাই, সেগুলো কিন্তু সিটি করপোরেশন আবার উঠিয়ে দেবে। আবার তাদেরও অনুমোদন লাগবে। তার পরও আমরা সিটি করপোরশনকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই।